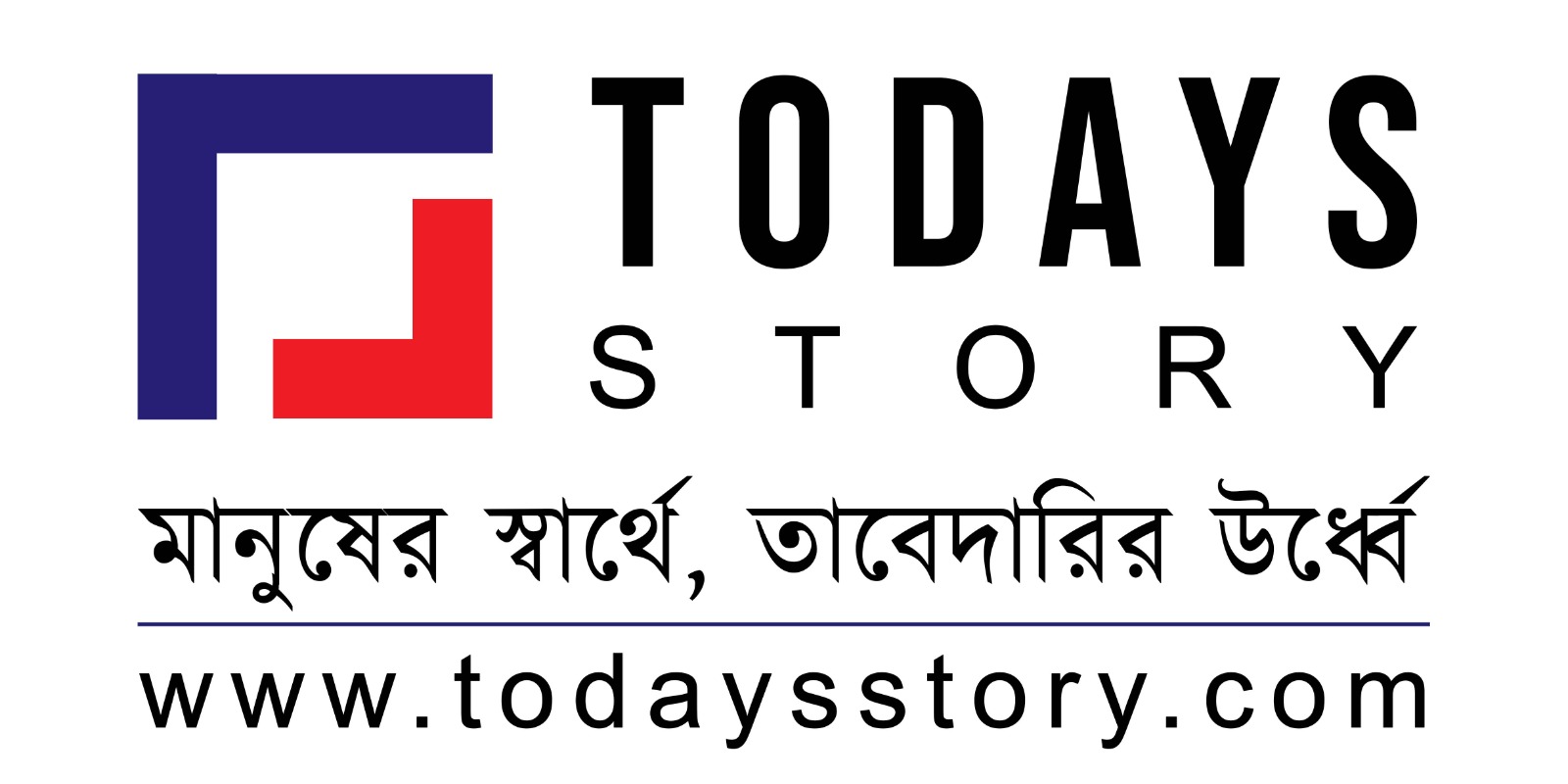📝শুভদীপ রায় চৌধুরী, Todays Story: বঙ্গের প্রথম সারির কালীমন্দিরের নাম করলেই যে মন্দিরের নাম সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয় সেটি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির। রানি রাসমনির প্রতিষ্ঠিত এই সিদ্ধপীঠে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয় দীপাবলিতে। দীর্ঘ সামাজিক লড়াইয়ের পর রাসমনি নির্মাণ করেছিলেন জগদীশ্বরীর এই মন্দির। পরবর্তীকালে জগদীশ্বরীই হয়ে উঠলেন সকলের ভবতারিণী।
প্রসঙ্গত, রাসমনির জন্ম ১৭৯৩ খ্রিঃ। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। সেই সময়ে হালিসহরে জন্ম রানি রাসমনির। তিনি জন্মেছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এক কৈবর্ত পরিবারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাসমনি সম্পর্কে বলেছিলেন, “রানি রাসমনি জগদম্বার অষ্টনায়িকার একজন। ধরাধামে তাঁহার পূজার জন্যই আসিয়াছিলেন।” রাসমনির সমগ্র জীবনে অমর কীর্তি “দক্ষিণেশ্বর মন্দির”, ঠিক তেমনি তাঁর অমর উপহার-“শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব”। ভারতের তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির- যার প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশ্লোকা রানী রাসমনি।
উল্লেখ্য, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ফরাসী ঐতিহাসিক ও জীবনীকার মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪) বিলেছিলেন-
“ঐ সময়ে নিম্ন শ্রেণীর একজন ধনী মহিলা ছিলেন, তাঁর নাম রানী রাসমণি। কলিকাতা হইতে প্রায় চার মাইল দূরে গঙ্গার পূর্বতীরে দক্ষিণেশ্বরে তিনি কালীর একটি মন্দির স্থাপন করেন। সেখানে পুরোহিতের কাজ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইতেছিল। তাছাড়া, এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন শূদ্রাণী। অবশেষে ১৮৫৫ সালে ঐ পদ গ্রহণ করিতে রামকৃষ্ণ মনস্থ করিলেন … ১৮৬১ সালে রাসমণির মৃত্যু হয়। রাসমণি ছিলেন “নয়া বড়লোক” এবং জাতিতে নিম্নশ্রেণীর। তাই তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তাঁহার মহানুভবতা ও উদারতার ফলে সকল ধর্মের অতিথিদের থাকার জন্য এখানে কয়েকটি কামরা ছাড়িয়া দেন।”
বলাবাহুল্য, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার আগেই রাসমনি জমি খোঁজ করছিলেন। আর তাঁর জন্মস্থান কুমারহট্ট হালিসহর ছিল প্রসিদ্ধ শাক্তভূমি। কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রধান এই হালিসহরের গোঁড়া সমাজপতিরা তাঁর ইচ্ছের মান দেননি। রানির অনুরোধে তাঁরা সদর্পে বলেন জেলের মেয়ের মন্দির তৈরির অধিকার নেই। আর বর্ণশ্রেষ্ঠরা বাঁধা দেওয়ার কেউ হালিসহরে জমি দিতে চাননি।
রাসমণি দেবী তাঁর স্বামীর স্মৃতিতে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির তৈরী করেন, যা তাঁর জীবনের সবথেকে বড় কাজ। বাংলার ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ধারক বাহক এই মন্দির। রাণি রাসমণি মন্দির স্থাপনের জন্য বারাণসী সমতুল্য গঙ্গার পশ্চিমদিকে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে জমি সংগ্রহের চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐ অঞ্চলের “দম আনি”, “ছয় আনি” জমিদাররা রাণির প্রচুর অর্থের বিনিময়েও কোন জমি বিক্রয় করতে চাননি। অগত্যা রাসমনিকে গঙ্গার পূর্বকুলেই দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্মাণ করতে হয়।
উল্লেখ্য, রাসমনি বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করলেও, তাঁর ধর্মমত ছিল উদার এবং তিনি ছিলেন একাধারে বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্তমতের অনুসারিণী। বাড়িতে গৃহদেবতা রঘুনাথ প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কালীঘাটে বাগানবাড়ি, পুষ্করিণী এবং আদিগঙ্গার পাকাঘর নির্মান করেন এবং সেখানে তিনি ব্রাহ্মণভোজন অনুষ্ঠান করতেন। রাসমনি দেবী অন্নপূর্ণা দর্শনে কাশীযাত্রার করেন। রাসমনি দেবীও জলপথে কাশীযাত্রায় স্থির করায়, সেই মতন ২৫ খানি নৌকা, ৬ মাসের উপযোগী দ্রব্যাদি, দাস-দাসী, দ্বারবান প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। এইভাবে ২৫টি বজরা প্রস্তুত করেন। পরের দিন কাশীযাত্রার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি রাত্রে নিজের ঘরে শুতে যান। সেই রাতেই তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে জগজ্জননী বলেন –“কাশী যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, ভাগীরথীর তীরে মনোরম স্থানে আমার মুর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করো। আমি ঐ মূর্তিতেই আবির্ভৃতা হয়ে তোমার নিত্যপূজা গ্রহণ করবো।“ স্বপ্নাদেশের পর রানি শয্যা ত্যাগ করে ভক্তিভরে জগন্মাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন এবং কাশীযাত্রা বন্ধ রেখে প্রতিমা তৈরিতে বদ্ধপরিকর হন এবং তাতে সফলও হন।
উল্লেখ্য, দক্ষিশ্বেরের নবরত্ন মন্দিরের গঠনশৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল বাওয়ালীর মন্ডল প্রতিষ্ঠিত টালিগঞ্জের রাধাকান্ত মন্দির (১৮০৯ সালে), পাথুরিয়াঘাটার ধনপতি দর্পনারায়ন ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মূলাজোড়-শ্যামনগর ব্রহ্মময়ী মন্দির (১৮০৮ সালে) ও লোকগাথা এবং প্রচলিত কথার সূত্রধরে টালিগঞ্জের পশ্চিম পুঁটিয়ারীতে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের নন্দদুলাল রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত করুণাময়ী কালীমন্দিরের গঠনশৈলী (১৭৬০ সালে)।
বলাবাহুল্য, কলকাতা থেকে ৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্বকূলে উত্তর চব্বিশ পরগনায় এই দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। “দক্ষিণেশ্বর” নামটির সঙ্গে তখনকার জনগনের বিশেষ পরিচয় ছিল না, গ্রামটির অবস্থা এখনকার মতন জনবহুল ছিল না। মাঝে মাঝে জঙ্গল, বাগান, পুষ্করিণী, কবরস্থান ছিল। এখানে স্থাপিত একমাত্র সরকারি বারুদখানা ম্যাগাজিনের, আর কিছু ইংরেজ ও স্থানীয় জমিদারদের ঘোড়ার গাড়ি যাতায়াত করত। হিন্দুদের সাথে কিছু মুসলমানের এবং ইংরেজের বসতিও ছিল। ইংরেজদের গির্জা না থাকলেও মুসলমানের “মাজার, “দরগা ছিল। বর্তমানে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছেই মোল্লাপাড়ায় একটি মসজিদও ছিল, যেখানে পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম সাধনের সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নামাজ পড়তে যেতেন।
বড়িশার প্রখ্যাত জমিদার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী বড়িশা থেকে এসে দক্ষিণেশ্বরে যখন বসবাস করা শুরু করেন তখন তাঁরাই এখানকার বনজঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রামটির উন্নতি সাধন করেন এবং বহু লোক এনে তাদের বসতি স্থাপন করেন। এই বংশেরই যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করেন এবং ত্যাগী সন্তানরূপে “স্বামী যোগানন্দ”নামে পরিচিত হন।
দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন মন্দির বাংলার শিল্পকলার এক অপূর্ব নিদর্শন।। মন্দিরের উচ্চতা একশো ফুট। গর্ভগৃহে কালো পাথরের বেদির ওপর রুপোর প্রস্ফুটিত শতদল। চারকোণে রুপোর স্তম্ভ। মা এখানে বেনারসী শাড়ি পরিহিতা, ত্রিনয়নী শ্যামাকালী। তাঁর অঙ্গে অসংখ্য স্বর্ণরৌপ্য অলংকার। বামদিকের একটি হাতে নৃমণ্ড ও অপরটিতে অসি। ডানদিকের দুটি হাতে বরাভয় মুদ্রা পদতলে শ্বেতপাথরের শিব। বছরে তিনদিন বড় পূজা হয় দক্ষিণেশ্বরে। দীপান্বিতা, রটন্তী ফলহারিণী কালীপূজো।শাস্ত্রমতে কালীপুজো করতে যেসব উপাচার লাগে সবই থাকে। মায়ের মন্দিরের উত্তরে রাধাকৃষ্ণদেবের মন্দির। উল্টোদিকে সারি দিয়ে বারোটি শিব মন্দির। তিন মন্দির তিন ধরনের স্থাপত্য। ভবতারিণীর নবরত্ন মন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির আটচালা মন্দির এবং রাধাকান্তের মন্দির ইউরোপীয় ধাঁচের। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে রানি রাসমনি সফল করেন তাঁর সর্বধর্ম-সমন্বয়ের স্বপ্ন। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের এক মহামিলন তীর্থ। ধর্মের এই তিন ধারাকে একসঙ্গে করা, এমন দুঃসাহসের কাজ সম্ভব হয়েছিল রাসমনির জন্যই। মন্দির সম্পূর্ণ হওয়ার পর মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন খুঁজছিলেন রানী। এমন সময় মায়ের প্রত্যাদেশ-“যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।”
রাসমনির দলিল থেকে জানা যায়, এখানকার মোট সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা স্থানটি ৪২ হাজার ৫০০ টাকায় কিনেছিলেন কুঠিবাড়িসমেত। এই কুঠিবাড়িটিই এই উদ্দানের আদি বাড়ি, যা সামান্য সংস্কারের পর এখনো অপরিবর্তিত আছে। গাজী সাহেবের পীরের স্থানটিও আদি। বাকিঘর বাড়ি-মন্দির-ঘাট ইত্যাদি রানির আমলে তৈরী।
১৮৪৭ সালে ৬ সেপ্টেম্বর “বিল অফ সেল” এর মাধ্যমে জমিটি কেনা হলেও সেটি তখন রেজিস্ট্রি করা যায় নি কারণ, তখন রেজিস্ট্রেশন আইন চালু ছিল না। পরে আইন বলবৎ হলে ১৮৬১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রানি রাসমনি সম্পাদিত আরেকটি দেবত্তর দলিলের মধ্যে ঐ “বিল অফ সেল”-এর কথা উল্লেখ্য করে, সেই দলিলটি ১৮৬১ সালের ২৭ আগস্ট আলিপুরের রেজিস্ট্রি করা হয়। রাসমনি যখন জমিটি কেনেন তখন তার চৌহদ্দি ছিল-পুর্বদিকে কাশীনাথ চৌধুরীদের জমি, পশ্চিমদিকে গঙ্গা, উত্তরদিকে সরকারি বারুদখানা আর দক্ষিণদিকে জেমস হেস্টির একটি কারখানা। জমি কেনার পর পূর্বদিকে লোকালয় গড়ে ওঠে, দক্ষিণদিকের অংশে জেমস হেস্টির কারখানা স্থলে পরে যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি স্থাপিত হয়েছিল।
দক্ষিণেশ্বরে জমি কেনার সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৪৭-৪৮ সাল থেকেই এখানকার যাবতীয় নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং সেই কাজ প্রথম দিকে রানীর প্রধান সহায়ক ছিলেন জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাস। পরে রানীর তৃতীয় জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের ওপরই এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, রানি মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকেই খোঁজ নিতেন। রাসমনি তৎকালীন খুব নামি বিলাতি ঠিকাদারি সংস্থা “ম্যাকিনটস অ্যান্ড বারন” কোম্পানিকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার চুক্তিতে মন্দিরের পোস্তা ও ঘাট তৈরীর কাজের ভার দেন। পোস্তা, বাঁধের কাজ শেষ হলে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর গঙ্গার দিকে একই নকসা অনুযায়ী একই ধাঁচের ১২টি শিবমন্দির ও চাঁদনি এবং এই মন্দিরগুলির পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত মাটির টালি বাঁধানো একটি বিরাট চতুষ্কোণ প্রাঙ্গন তৈরী করা হয়, যার আয়তন ৪৪০ ফুট লম্বা এবং ২২০ ফুট চওড়া। মন্দিরের সমগ্র এলাকার তিনপাশে দালানবাড়ী তৈরী করা হয়। এই বাড়িগুলির মাঝখান দিয়ে মন্দিরে আসার জন্য তিনটি প্রবেশ পথও করা হয়। একই সঙ্গে কালীমন্দির ও বিষ্ণুমন্দিরের কাজ চলতে থাকে। মন্দির এলাকার বাইরে উত্তরে একটি নহবতখানা এবং দক্ষিণে অনুরূপ একটি নহবতখানা তৈরি করা হয় এবং এলাকাটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়।
সমগ্র মন্দিরটি নির্মাণ করতে প্রায় ৯ বছর সময় লেগেছিল। এখানে মা-কালী, শিব, রাধাকৃষ্ণের মন্দিরাদি স্থাপিত হলেও এটি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির নামেই প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মান শুরু হয় ১৮৪৭-৪৮ সালে এবং সমাপ্তি হয় ১৮৫৪ সালে। প্রতিষ্ঠার দিন অপরূপ সাজে সাজানো হল মন্দির চত্বর। বড়ো বড়ো ঝাড়বাতি দেওয়া হল বিশাল নাটমন্দিরে। দেবীর গলায় চিক, মুক্তোর সাতনরী হার, সোনার মুন্ডমালা। কানে কানপাসা, ঝুমকো চৌদানী, নাকে নথ ও নোলক। নীচের বামহাতে ধরা নৃমুণ্ড, উর্ধ্ব বামহাতে অসি, ডানহাতে বরাভয়। রানিমা মনের মতন করে মাকে সাজিয়েছিলেন। সকল কাজ ঠিকমতো শেষ হওয়ার পর, রাসমনি যখন মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং দেবীকে অন্নভোগ দেওয়ার জন্য সচেষ্ট তখনও তিনি জাতিতে শূদ্র হওয়ায় প্রথা অনুযায়ী কোন ব্রাহ্মণই এমনকি রানীর নিজের গুরুদেবও মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দেবীকে ভোগ দিতে রাজি হলেন না। সেইজন্য রানী বিভিন্ন চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের কাছে বিষয়টির শাস্ত্রনুযায়ী বিধান জানবার জন্য অনুরোধ করায় সবাই এই কাজকে অশাস্ত্রীয় বলেন। একমাত্র কলকাতার ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন প্রতিষ্ঠার আগে যদি কোন ব্রাহ্মণকে ঐ মন্দির দান করা যায় এবং সেই ব্রাহ্মণ যদি ঐ মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন তবেই তা অশাস্ত্রীয় হবে না।
এই বিধান দেওয়ায় রামকুমারকে বহু গোঁড়া ব্রাহ্মণ অভিযোগ করতে শুরু করেন, সেই কথা তিনি গ্রাহ্য করতে রাজি ছিলেন না। সেই সময় রাসমনি রামকুমারকেই এই কাজ করার জন্য আহ্বান করেন, রামকুমারও সেই কাজে ব্রতী হয় এবং অপরিণত কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে নিয়ে রাসমনির ইচ্ছানুয়ায়ী ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৮ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিন (১৮৫৫ সালে) মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।
উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণেশ্বরের মায়ের নাম-“জগদীশ্বরী”। দেবোত্তর দলিলেও এই নামেই রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য়ের বিষয় সর্বত্র মা ভবতারিণীর নামেই উল্লিখিতা। বেদীর উত্তর-পূর্ব কোণে মায়ের রৌপ্য নির্মিত পালঙ্গ। পালঙ্কের ওপর রয়েছে শয়নের যাবতীয় উপকরণ। এদিকে মায়ের সংসার, তৈজসপত্র। সেখানে রয়েছে রুপোর কলস, হাঁড়ি, থালা-বাটি, চামচ, পানের বাটা ইত্যাদি।
প্রতিদিন ৪টের সময় মায়ের সকালের আরতি হয়। সেই সময়ে মায়ের বাল্যভোগ মাখন ও মিছরি। এরপর মন্দির বন্ধ থাকে, ফের খোলা হয় সকাল ৬টায়। তারপর মায়ের স্নান আরতি। সকাল ৯টায় নৈবেদ্য ভোগ। বেলা ১২টায় অন্নভোগ। অন্নভোগে থাকে দুটি তরকারি, তিনরকমের ভাজা, ডাল, চাটনি, পায়েস এবং মাছ। এরপর মন্দির বন্ধ। আবার মন্দির খোলে সাড়ে ৩টে। তখন ফল, ছানা সহযোগে বৈকালি দেওয়া হয় ও রাত্রি ৮টায় হয় শীতল ভোগ। এছাড়া বিশেষ করে কার্তিক অমাবস্যা, বাসন্তী পুজোর দিন, জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন, সাবিত্রী চতুর্দশীর দিন, রটন্তী কালীপুজোর দিন, মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনও বিশেষ পুজো হয়।
এছাড়া, রাসমনির জন্মদিনে দুপুরে দৈ-মিষ্টি দিয়ে বিশেষ ভোগ দেওয়া হয় আর রাতে বিশেষ ব্যবস্থা। মায়ের জন্য আমিষ ভোগের ব্যবস্থাও থাকে। কেবলমাত্র একজন সেবায়েতের পালায় নিরামিষ ভোগ দেবার রীতি রয়েছে। সেকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার আগের দিন মন্দির প্রাঙ্গনে যাত্রাগান, কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণপাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছিল। পরের দিন দেবালয়ের বিশাল প্রাঙ্গণ ভোর থেকেই অসংখ্য ভক্তসমাগম হয়েছিল। রাসমনির আহ্বানে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, মূলাজোর, নোয়াখালি, বিক্রমপুর, চট্টোগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মন ছাড়াও কাশী, পুরী, মাদ্রাজ, পুনা, কনৌজ, মিথিলার ব্রাহ্মণরাও উপস্থিত ছিলেন, যার সংখ্যা লক্ষািধিক। এই ঐতিহাসিক মহোৎসবে রাসমনি “অন্নদান যজ্ঞ”-এর আয়োজন করেছিলেন। পূজানুষ্ঠান ছাড়াও এদিন “দধি-পুষ্করিণী”, “লুচি-পাহাড়”, “মিষ্টান্ন-স্তুপ”, “পায়েস-সমুদ্র”, “ক্ষীর-হ্রদ, “দুগ্ধ-সাগর”, “ঘৃত-কূপ”, “মৃন্ময়পাত্র-স্তুপ” প্রভৃতির মধ্যদিয়ে রানিমা “অন্নদান–যজ্ঞ”এর বিশাল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে একদিনেই রাসমনির কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। এই বিরাট অনুষ্ঠানে পুরোহিতগণের মধ্যে গৌড়াদ্য-দ্রাবিড় বৈদিকগণও যেমন ছিলেন, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণরাও ছিলেন। রামকুমারই দেবীকে অন্নভোগ দিয়েছিলেন এবং হোমও তিনি করেছিলেন বলেই “লীলাপ্রসঙ্গ”এ উল্লেখ আছে।
বলাবাহুল্য, যে সমস্ত বঙ্গীয় বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণরা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন-রামসুন্দর চক্রবর্তী, উমাচরণ ভট্টচার্য্য, বৈকুন্ঠনাথ ন্যায়রত্ন, চণ্ডীচরণ বিদ্যাভূষণ, কেশবচন্দ্র তর্কবাগীশ, ঠাকুরদাস বিদ্যালঙ্কার, রামকুমার তর্কারঙ্কার, পীতাম্বর চূড়ামণি, যদুনাথ সার্বভৌম, মধুসূদন তর্কালঙ্কার, সীতারা বিদ্যাভূষণ, বৈকুন্ঠ ন্যায়রত্ন, কৃত্তিবাস তর্করত্ন, রাইচরণ ভট্টাচারার্য্য, প্রেমচাঁদ বাচস্পতি, ঈশানচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, ভোলানাথ সার্বভৌম, ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি, ব্রজনাথ চক্রবর্তী, বানেশ্বর বিদ্যাভূষন, চিন্তামণি বিদ্যাসাগর, নবকুমার শিরোমণি ইত্যাদি।
মন্দির প্রতিষ্ঠার মহোৎসব সমাপ্ত হলেও বরাবরের জন্য রানি মা কালীর পূজকপদে সৎসাহসী ও শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমারকেই মনোনীত করায়, রামকুমার দক্ষিণেশ্বরেই থেকে যান এবং পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ ভাই গদাধরও তাঁর সঙ্গে বাস করতে থাকেন। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পূজার ভার দেওয়া হয় ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। এইভাবেই শুরুতেই মা কালী এবং রাধাকৃষ্ণের মন্দির দুটির পূজার ভার রাঢ়ীশ্রেণীর “চট্টোপাধ্যায়” পদবিধারী দুই ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন আর দ্বাদশ শিবমন্দিরের পূজার ভার দেওয়া হয় বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণদের। এর মধ্যে উমাচরণ ভট্টচার্য্যও ছিলেন।
রাসমনির ঐতিহাসিক সৃষ্টি- দক্ষিণেশ্বর মন্দির, কালীপুজোয় লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম ভবতারিণী মন্দিরে