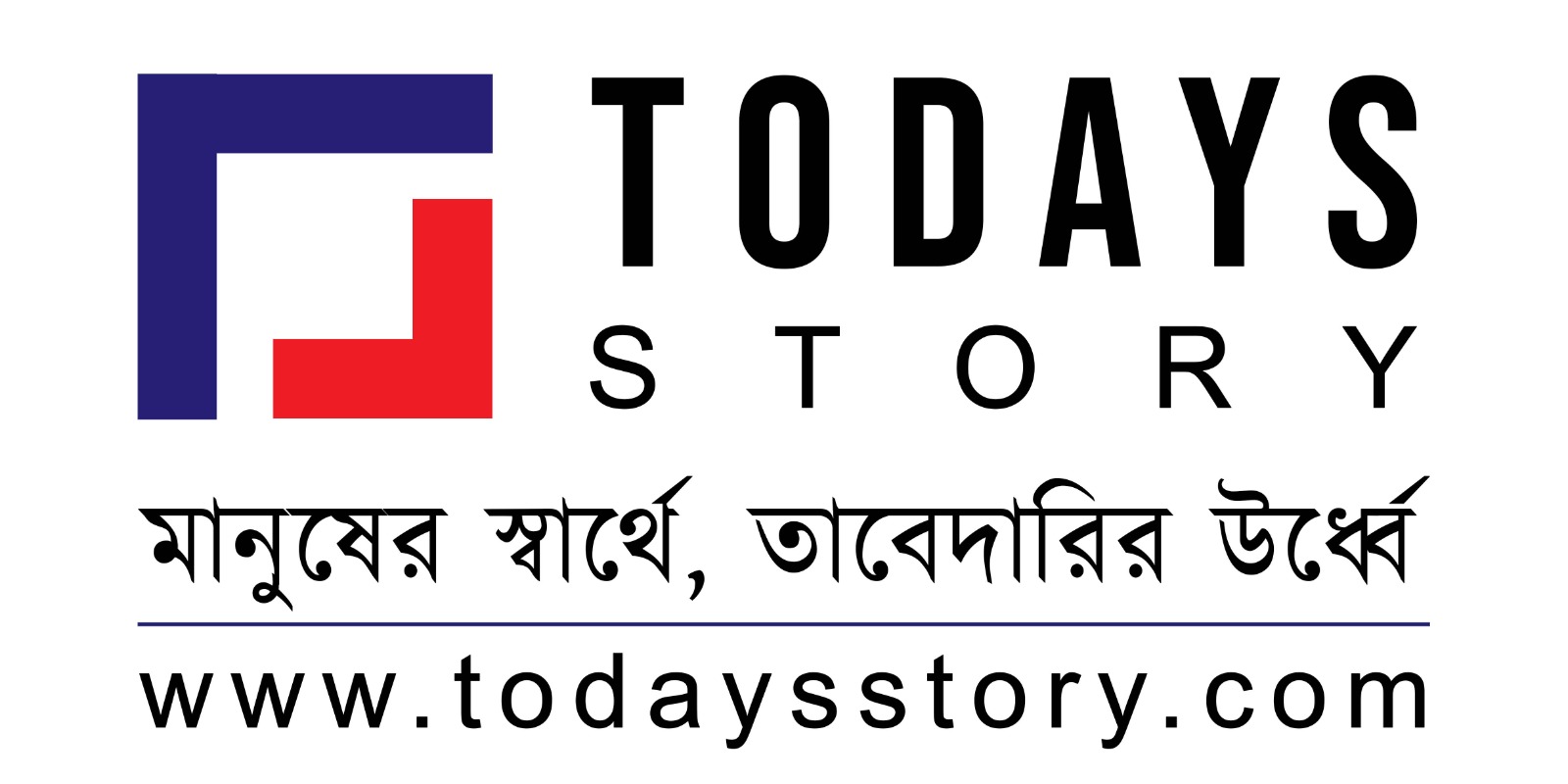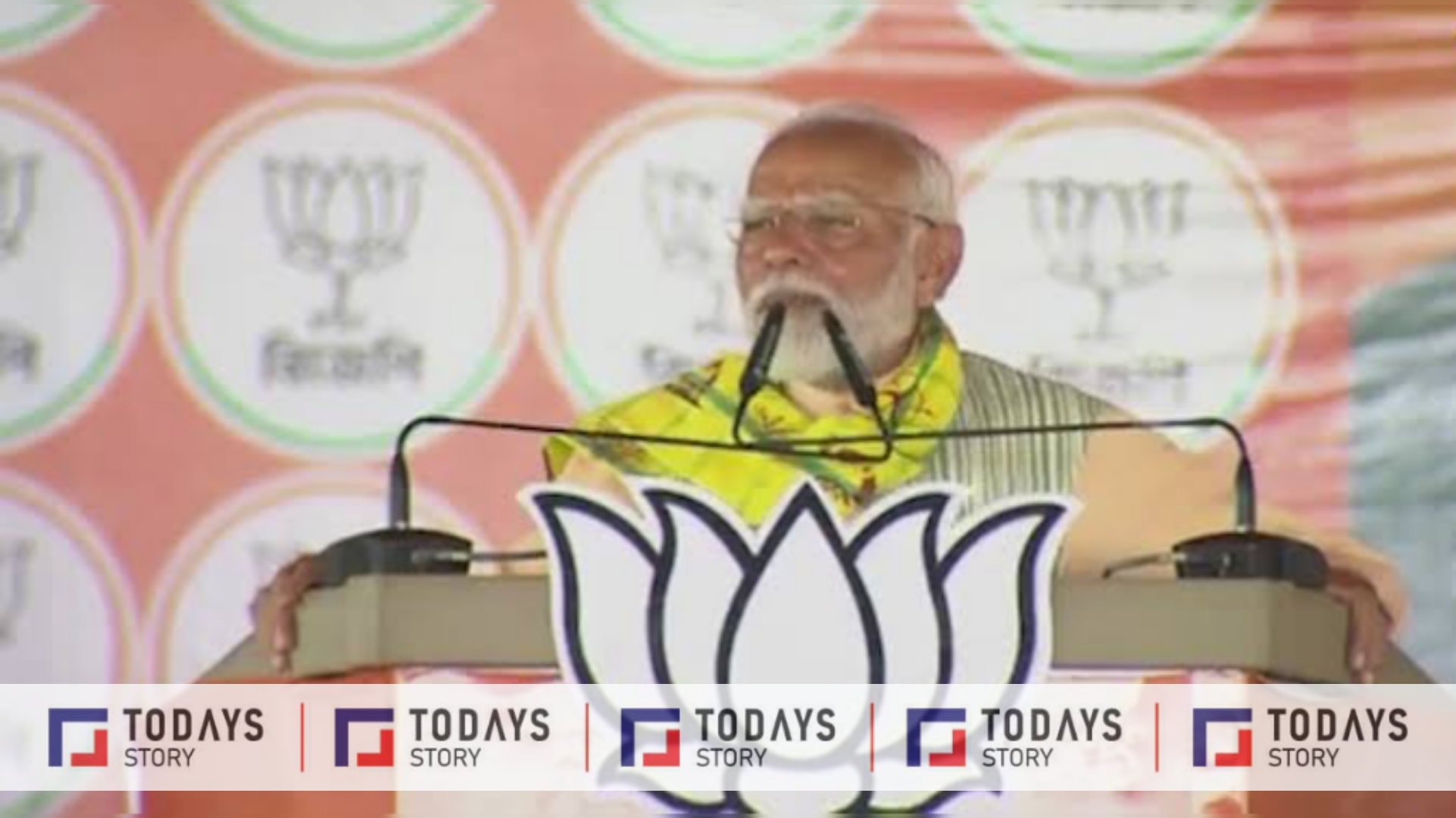📝 নিজস্ব সংবাদদাতা, Todays Story: ‘লোকটা নিজেই একটা গান/ আস্ত একটা গান’! কবীর সুমন (তখন ‘চট্টোপাধ্যায়’) এক মঞ্চানুষ্ঠানে গেয়ে শোনালেন এমনই এক গান। তাঁর গানের সঙ্গে ছিল সেই ‘আস্ত একটা গান’ মানুষটির অনুষ্ঠান। মঞ্চে উঠলেন এক কাঁচাপাকা চুলের প্রৌঢ়। নিবু নিবু আলো জোরালো হয়ে উঠতেই দেখা গেল অতি সাদামাঠা পোশাকে এক মানুষ যেন আপিসফেরতা মিনিবাসের সিট থেকে উঠে হঠাৎই মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন। কোনও যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়াই গেয়ে উঠলেন— ‘দারুণ গভীর থেকে ডাক দাও’।
তদ্দিনে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন শ্রোতাবৃত্তে। বাংলা গানের নদীতে তখন নতুন জোয়ার। সুমনের আবির্ভাবের পর বাঙালির স্মৃতিরেখায় টান পড়ছিল— আর কারা গেয়েছেন এমন ছকভাঙা গান? গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ‘মহীনের ঘোড়াগুলি’, ‘নগর ফিলোমেল’, ‘রঞ্জন প্রসাদ’ প্রমুখের সঙ্গে আরও একটা নাম ভাসছিল নব্বইয়ের দশকের হাওয়ায় হাওয়ায়। প্রতুল মুখোপাধ্যায়। বাংলা গানকে ঘিরে তখন অনেক মিথ। প্রতুল সেই কিংবদন্তির অন্যতম চরিত্র।
জন্ম অবিভক্ত বাংলার বরিশালে। ১৯৪২ সালে। বাবা প্রভাতচন্দ্র ছিলেন স্কুলশিক্ষক, মা বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় গৃহবধূ। দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়। স্কুলে পড়াকালীনই তাঁর এক আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পান নিকটজনেরা। মাত্র ১২ বছর বয়সে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমি ধান কাটার গান গাই’ কবিতাটিতে সুরারোপ করে বন্ধুদের চমকে দিয়েছিলেন প্রতুল। পাশাপাশি নিজেও লিখতে থাকেন ছড়া, গানের লিরিক। চাকরি করেছেন আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত গেরস্তের মতোই। কিন্তু সেই গেরস্তালির মধ্যেই কোথাও যেন আগুন ছিল। ধিকিধিকি গানের আগুন। বিপ্লব, স্বপ্নভঙ্গ আবার বিপ্লব আর আবার স্বপ্নভঙ্গের বঙ্গীয় রাজনীতির অনেক উথালপাথালের সাক্ষী প্রতুল রাজনৈতিক বিশ্বাসে ছিলেন সমাজতন্ত্রের শরিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোধ হয় মানুষ আর মানবতাকে তাঁর গানে সবার আগে রাখতেন।
কোনও যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়াই শুধুমাত্র ‘বডি পারকাশন’ ব্যবহার করে গানের রেওয়াজ গণনাট্যের গানেও ছিল না। বরং সেখানে গান ছিল যূথবদ্ধ মানুষের হারমনির উপরে দাঁড়িয়ে। ‘কয়্যার’ বা যৌথ গানের সঙ্গে মানুষের অধিকার অর্জনের লড়াই বা দিনবদলের স্বপ্ন ইত্যাদির অঙ্গাঙ্গি যোগ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতুল সে রাস্তায় হাঁটলেন না। তাঁর গান সে অর্থে তাই ‘গণসঙ্গীত’ হয়েও যেন হল না। এমনকি, মঞ্চে গাওয়ার সময়েও (মঞ্চের বাইরেও হাটে-মাঠে-ঘাটে) কোনও যন্ত্রীকে সঙ্গে নিলেন না। কখনও নিজের গাল, কখনও বা বুক বাজিয়ে, তুড়ি দিয়ে, হাততালি দিয়ে গাইতে লাগলেন নিজের বাঁধা গান। গায়ক একা হয়েও যেন একা নন। তাঁর সঙ্গী তাঁরই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। প্রতুলের গান গণনাট্যের গানেরই উত্তরাধিকার হলেও তার থেকে তার স্বাতন্ত্র্য প্রধানত ওই এক জায়গাতেই।
এরই সঙ্গে প্রতুল গেয়েছেন ছোটদের জন্য। ‘কুট্টুস কট্টাস’ নামের অ্যালবামে প্রায় প্রতিটি গানে রয়েছে কেমন এক সস্নেহ প্রশ্রয়ের টান। সুমন-নচিকেতা-অঞ্জনের ‘ছোট বড় মিলে’ আর প্রতুলের এই অ্যালবামই কি বাংলার শেষ ‘ছোটদের গান’? যে কাজ সলিল চৌধুরী শুরু করেছিলেন অন্তরা চৌধুরীকে দিয়ে, সেই কাজটি ছিল ছোটদের ‘বড়’ হয়ে ওঠার জন্য গান বাড়িয়ে দেওয়ার কাজ। প্রতুল তাঁর সেই অ্যালবামে সেই কাজেরই উত্তরাধিকার বইলেন।
একাধিক সাক্ষাৎকারে প্রতুল বলেছেন, সঙ্গীতের প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। তাঁর ভাষায়, “আমি শুনে শুনে, ঠেকে ঠেকে শিখেছি।” তাঁর শ্রোতাদেরও প্রথমে হোঁচট খেতে হয়েছিল তাঁর গান শুনতে বসে। একজন মানুষ কণ্ঠ, প্রশিক্ষণ, পরিমার্জন— সব কিছুকে পাশে সরিয়ে রেখে কী করে হয়ে উঠছেন ‘আস্ত একটা গান’, তা আগামী প্রজন্মকে ভেবে উঠতে গেলেও ভাবনার জিমন্যাশিয়ামে ভাবা প্র্যাকটিস করতে হবে। কী করে সম্ভব হয়েছিল তা, এখন আর মনে পড়ে না নব্বই দশকে যুবক হয়ে উঠতে থাকা প্রজন্মের। মাথার উপর এক স্থবির রাজনীতি আর তার সুবাদে চারিপাশে ‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’-সুলভ একটা ‘ফিল গুড’ ভাবকে যে হাতেগোনা কয়েক জন দুমড়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রতুল অন্যতম।
হয়তো সেটা ‘সময়ের দাবি’। কিন্তু সময় কি তার পরে আর দাবি জানাতে পারল না? ‘আমি বাংলায় গান গাই’ পরে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা মূলধারার সিনেমায়। সেখানে সে গানের ধার কেমন যেন ভোঁতা। ‘দৃপ্ত স্লোগান’ আর ‘তৃপ্ত শেষ চুমুক’-কে ধরতে পারেনি উত্তর-বিশ্বায়ন পর্বের বাংলা বা বাঙালি। বাংলা গানের নব্বইয়ের ‘নবজোয়ার’ স্তিমিত হয়ে এসেছিল মিলেনিয়াম পর্বেই। তবু কখনও বইমেলার মাঠে লাউডস্পিকারে বেজে উঠত ‘ডিঙ্গা ভাসাও’ বা ‘ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ’। এখনও বাজে বোধ হয়। আগামী দিনেও বাজবে। কিন্তু সেই গানের আত্মাটি সম্ভবত থাকবে না। কারণ, সেই গানমানুষের সৃষ্টি অ্যালবামে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাকে তিনি নিজের সঙ্গে করেই নিয়ে গেলেন। তাঁর গান ছিল আক্ষরিক অর্থেই নগর কবিয়ালের গান। যে কোনও আসরে অথবা আসর ছাড়াও গেয়ে ফেলা যেত। বাস্তবে আজীবন রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন প্রতুল। সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলনের কালেই তাঁরা গানের জারণ। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে তাঁকে দেখা গিয়েছে। সম্ভবত প্রতিবাদকেই গান আর জীবনের সঙ্গে একাত্ম করতে চেয়েছিলেন প্রতুল।
বব ডিলান তাঁর একটি গানে নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, “ওভার এক্সপোজ়ড, কমার্শিয়ালাইজ়ড/ হ্যান্ডল উইথ কেয়ার।’’ প্রতুল সেই ‘কেয়ার’টিকেই কেয়ার করেননি কখনও। তাঁর গান ভেসে থাকল বাংলার বুকে পলাশফুলের ঝরে পড়া পাপড়ির মতো। যা হাওয়ায় ভাসে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। তার সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে গেলে যেতে হয় পড়ে থাকা ফুলের কাছেই। হাতে তুলে নিলে তারা গান হয়ে যায়, কবিতা হয়ে যায়, স্বপ্ন হয়ে যায় দিনবদলের। কিন্তু তার জন্য ওই যে, “যেতে হবে!” দূরে, বহু দূরে, আরও, আরও দূরে…।