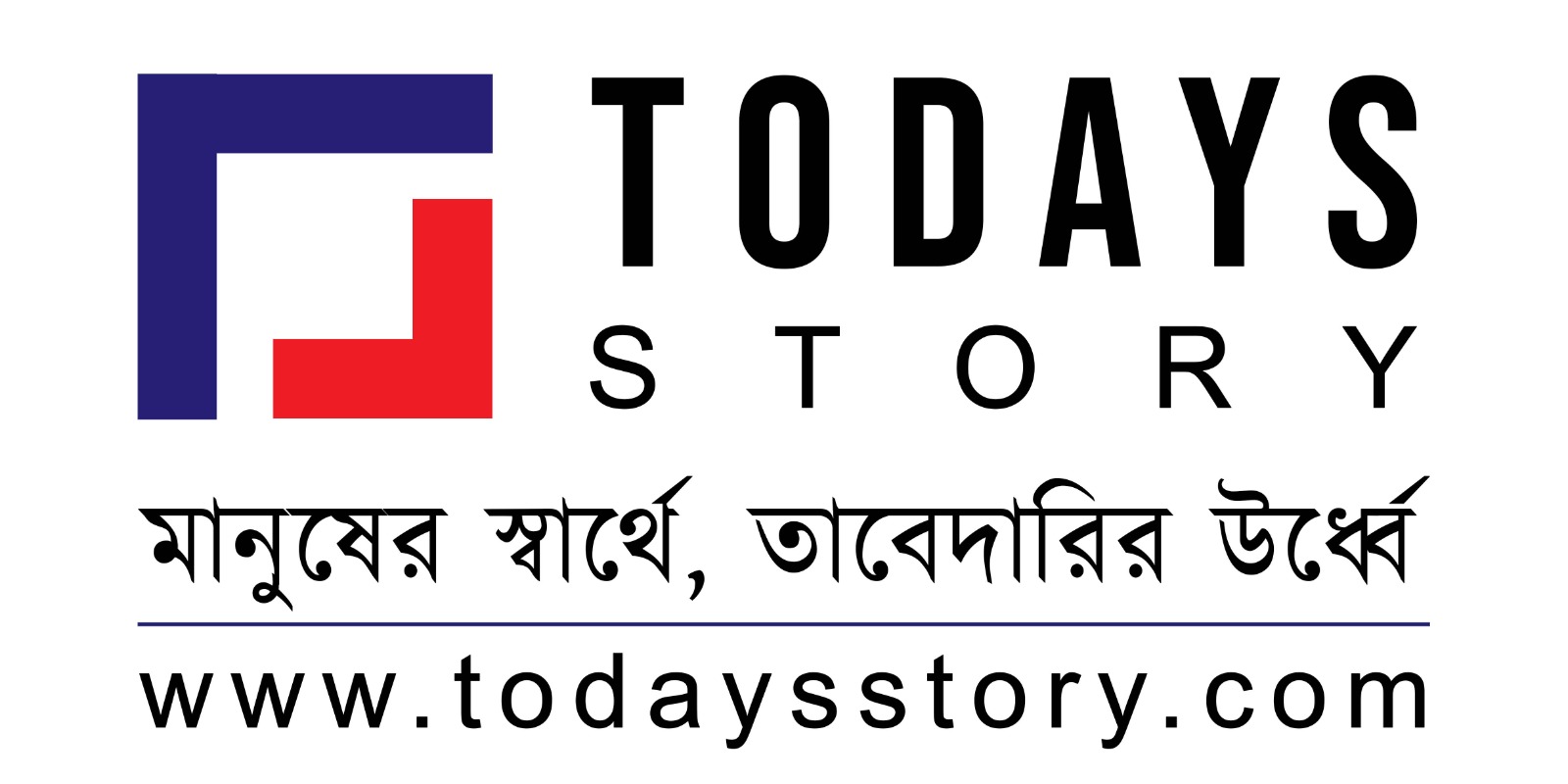📝শুভদীপ রায় চৌধুরী, Todays Story: বনেদি বাড়ির পুজোগুলির অন্যতম এবং সবচেয়ে প্রাচীন পুজো এটি। বাংলার ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিকতার সঙ্গে এই পরিবারের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাই শারদোৎসবের প্রাক্কালে এই বাড়ির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা না করলে বাঙালির প্রাণের দুর্গাপুজো কোথাও যেন ফিকে হয়ে যায়। তাই বাংলার ঐতিহ্যের কথা বললেই যাদের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তাঁরা হলেন মল্লরাজা।
এক সময় জয়পুরের রাজপুত রাজা নৃসিংহ দেব সপরিবারে শ্রীক্ষেত্র পুরীতে, তীর্থভ্রমণে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সন্তান সম্ভবা স্ত্রী রাণী রত্নাবলী দেবী। মহারাজের ইচ্ছা যে, পুরীতেই যেন রাণীমা তাঁর সন্তানের জন্ম দেন। কারণ, অতীতে বেশ কয়েকটি সন্তান জন্মের পরে বেশীদিন বাঁচেনি। তাই রাজা মানসিক করেছেন জগন্নাথের কাছে, যদি সন্তান দীর্ঘজীবী হয়, তাহলে শ্রীক্ষেত্রকে সোনায় মুড়ে দেবেন তিনি। তবে তাঁর আরও একটি বাসনা, জগন্নাথধামেই যেন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।
তবে সস্ত্রীক রাজার সঙ্গে তাঁদের অগণিত সৈন্যসামন্ত, লোকলস্কর, দাসদাসী সকলেই পৌঁছে গেলেন পুরীতে। মূলত, সন্তানসম্ভবা রাণীমা রয়েছেন, তাঁর বিশেষ যত্নেরও প্রয়োজন। তাই পথে কোনোরকম যাতে অসুবিধায় না পড়তে হয়, তাই রাজার এই আয়োজন। সেই সময় বেশ অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছেন, আর চন্দনেশ্বরের কাছাকাছি আসতেই রাণীমা’র অবস্থা আরও অবনতি হয়। যাত্রার ধকল তিনি আর নিতে পারছেন না। মহারাজও বেশীদূর এগোতে সাহস পেলেন না৷ তাই সেই সময় স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ হরিহর মিশ্রের বাড়ীতেই কয়েকজন দাসী সমেত রাণীমাকে রেখে এগিয়ে গেলেন পুরীর পথে। যাবার আগে, রাণীর পাহারায় এক বিশ্বস্ত সৈন্যকে রাখলেন যাতে সন্তান জন্মের খবর ঠিক সময়েই মহারাজ পান। রাণীকেও আস্বস্ত করে গেলেন, জগন্নাথের প্রসাদ নিয়েই ফিরবেন।
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন পরিচর্যায় রাণী বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং সঠিক সময়ে ৬৭৭ খ্রীস্টাব্দ, ২রা এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, রামনবমীর দিন এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ শিশুটিকে দেখেই চমকে ওঠেন। এ’যে অসম্ভব, এমন শিশু মানুষের গর্ভে কীভাবে জন্মায়? এ যে দেবশিশু! কপালে স্পষ্ট অর্ধচন্দ্রের ছাপ, হাত-পায়ের তালুর রেখাও শুদ্ধ স্পষ্ট! আর সন্তান জন্মাবার পরই প্রহরী ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন রাজাকে খবর দিতে হবে।
কিন্তু, শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছানোর আগেই দেখা হয় বাকি প্রহরীদের সঙ্গে। সকলেই সেদিকেই আসছেন। কিন্ত কেন? কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই, সবার মুখ থমথমে। কী হয়েছে? আজ আনন্দের দিন, রাণীমা পুত্রের জন্ম দিয়েছেন, সবাই আনন্দ করো। সবশেষে, মৌন ভঙ্গ করে সেনাপতি অকালে বজ্রপাতের মতোই বললেন, মহারাজ গতদিন বিকালে নরেন্দ্র সরোবরে সর্পাঘাতে মারা গিয়েছেন।
এই খবর রাণীর কানে তিনি শোকে বিহ্বল হন। ওদিকে মহারাজের মৃত্যুর খবর তীরের বেগে রাজধানীতে পৌঁছায়। সুযোগসন্ধানী মন্ত্রী সিংহাসন দখলে ব্যস্ত হয়ে পরেন। তীর্থ ফিরত সৈন্যরা, সদ্যোজাত রাজপুত্রকে কালসর্প জ্ঞানে সেই ব্রাহ্মণের কাছেই ছেড়ে যায়। আর ব্রাহ্মণের পরিচর্যায় আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে পুত্র সন্তানটি। রামনবমীতে জন্ম, তাই তার নামকরণ করা হয় রঘুনাথ। আশ্রিত যে উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়সন্তান, সে কথা ব্রাহ্মণ জানতেন, তাই অল্পবয়সেই ‘মল্ল যুদ্ধ’ পাঠের আখড়ায় ভর্তি করান। সঙ্গে চলতে থাকে বিভিন্ন শাস্ত্রের পাঠ। খুব অল্প বয়সেই রঘুনাথ শস্ত্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।
হঠাৎই একদিন শোনা যায়, রাজ্যের মহারাজ বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তিনি নিঃসন্তান। তাই সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আহ্বান জানিয়েছেন রাজধানী প্রদ্যুম্নপুরে(বর্তমান বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলার সীমানা)। সেই সময় পণ্ডিত হরিহর’ও তরুণ রঘুনাথকে নিয়ে উপস্থিত হন রাজ দরবারে। আলোচনা সভায় সকলের পরামর্শ ও বক্তব্য রাখার মাঝেই মহারাজের নজর পড়ে, রঘুনাথের উপরে। অল্পবয়স্ক এই তরুণের শক্তি, গাম্ভীর্য্য ও বিচক্ষণতা রাজাকে বারবার মুগ্ধ করতে থাকে। অবশেষে, আলোচনা সভা অসময়ে স্থগিত রেখেই মহারাজ, পণ্ডিত হরিহরের কাছে রঘুনাথকেই চেয়ে বসেন। ব্রাহ্মণও মনে মনে এটাই চেয়েছিলেন। রঘুনাথকেই দত্তক নিলেন মহারাজ। প্রকাশ্যে অভিষেক করলেন যুবরাজকে। যুবরাজ রঘুনাথের তখন ১৭ বছর বয়স।
উল্লেখ্য, এর ঠিক পরের বছরই যুবরাজ রঘুনাথকে রাজ্যাভিষেক করে মহারাজ ঘোষণা করা হয়। এরপরেই নিজস্ব শাস্ত্রশিক্ষা ও মল্লযুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ করে মহারাজ এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গ, প্রাগ-জ্যোতিষ, বরেন্দ্র, নালন্দা, রাজগীর হয়ে সুদূর কণৌজ পর্যন্ত নিজের রাজত্বের সীমানা সুরক্ষিত করেন। এরপরেই নিজে “আদি মল্ল” উপাধি গ্রহণ করেন এবং রাজধানীর নামকরণ করলেন “মল্লভূম”। কালের নিয়ম সবকিছুই নিয়মমাফিক চলতে লাগলো। জয়মল্ল, বেণুমল্ল, যাদবমল্ল, জগন্নাথমল্ল, বিরাটমল্ল প্রমুখ মহারাজের সময়কাল পেড়িয়ে এবারে, মহারাজ রঘুনাথের ঊনবিংশতম উত্তরসূরী মহারাজ জগৎমল্ল(৯৯৪ খ্রীস্টাব্দ-১০০৭ খ্রীস্টাব্দ)-এর আমল।সিংহাসনে বসার দিন থেকেই মহারাজ জগৎমল্ল শাসক হিসাবে প্রজাদের মনে আলাদা স্থান করে নিয়েছিলেন। রাজবংশের ইতিহাস অনুযায়ী, জগৎমল্লের আমলই মল্লবংশের সুবর্ণযুগ শুরু হয়। রাজ্যের বিস্তার থেকে শুরু করে সুশাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্থাপত্যকর্ম তথা রাজধানীর নিত্য জলকষ্ট দূরী করতে বিরাট জলাধার নির্মাণ ইত্যাদি সবই জগৎমল্লের কীর্তি। মহারাজ নিজেও মাঝেমধ্যেই ছদ্মবেশে বেড়িয়ে পড়তেন রাজ্য পরিদর্শনে। এইরকমই একবার রাজ্য পরিচালনায় সুষ্ঠু নিয়মানুবর্তীতা কোথায় পালিত হচ্ছে, না হচ্ছে সে সব দেখতে কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকজন নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন। পথেই সন্ধ্যা হওয়ায়, দামোদরের দক্ষিণকূলে বনবিষ্ণুপুর জঙ্গলেই থামার সিদ্ধান্ত নেন। কর্মচারীরা শিবির তৈরী করতে ব্যস্ত, ওদিকে রাজা, জঙ্গলের গভীরে গেছেন, পশু শিকারের জন্য। দূর থেকে একটি হরিণ দেখতে পেয়েই ধনুকের সজোড়ে তীর মারলেন। তীরবিদ্ধ হরিণ ছুটে যেতেই রাজাও তার পিছু নিলেন। কিছুটা গিয়ে দেখলেন, হরিণটি একটা বটগাছের নীচে ছটফটিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে এবং আচমকাই সেই বেলগাছ থেকেই এক নারীমূর্তির উদয় হয়। তিনি তীরবিদ্ধ হরিণের তীর বের করে ক্ষতস্থানে হাত বোলাতেই হরিণ উঠে দাঁড়ায়।
বলাবাহুল্য, এই দৃশ্য দেখে রাজামশাইয়ের বাকশক্তি বন্ধ হয়। কিছু পরে, সম্বিত ফিরে পেয়েই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন সেই নারী পা দু’টি। বহু সাধাসাধির পরে অগত্যা, সেই মাতৃহীন সন্তানের উপর কৃপা করেন কৃপাময়ী। দশভূজা কাত্যায়ণী স্বরূপ দেখালেন তাঁর সন্তানকে। মাতৃদর্শনের আনন্দে আত্মহারা মহারাজ জগৎমল্ল চোখের জলে দেবীর পা জড়িয়ে মিনতি করে চলেছেন, আর তোমায় ছাড়ছি না মা। আমার কাছেই তোমাকে থাকতে হবে। দেবী সম্মতি দিলে, মহারাজ তৎক্ষনাৎ মনস্থির করেন, রাজধানী স্থানান্তরিত করবেন। প্রদ্যুম্নপুর থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে এলো, বনবিষ্ণুপুরে। জঙ্গল পরিষ্কার করে তৈরি হল স্থায়ী বসতি। শুধু কাটা হলোনা সেই বটগাছটি।
এবার রাজ্যের বাছাই করা মৃৎশিল্পী এনে, গঙ্গামাটি দিয়ে তৈরী করানো হলো, রাজার সম্মুখে প্রকট হওয়া চিন্ময়ী মায়ের সেই মৃন্ময়ী বিগ্রহ। সেই বটগাছের সামনেই তৈরী হলো মন্দির। কথিত আছে, প্রথম মন্দিরটি মাটির তৈরী ছিলো। কীভাবে দশভূজার আরাধনা হবে, সেই বিধান জিজ্ঞেস করায় রাজপুরোহিত বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ ও কালিকা পুরাণে উল্লিখিত দুর্গোৎসবের নিয়ম বললেন। সেই থেকে শুরু হ’লো, বঙ্গদেশের প্রথম আনুষ্ঠানিক শারদোৎসব।
সালটা ৯৯৭ খ্রীস্টাব্দ। রাজার ইচ্ছা ছিলো, তাড়াতাড়ি দেবীর মূর্তি ও মাটির মন্দির করালেও, শারদোৎসবের পরেই পাকা মন্দির ও বিগ্রহ তৈরী করাবেন। পাকা মন্দির নির্মাণ করালেও, দেবীর বিগ্রহ পাল্টানোর সময়েই রাজা বাধা পান। যে মূর্তিতে একবার মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়েছেন, সেই মূর্তি পাল্টাতে গেলে তো, মা’কে বিসর্জ্জন দিতে হবে! সেই সময় রাজার মানসপটে ভেসে ওঠে দেবীর প্রতিকৃতি। আদেশ দেন যে, যেমন আছে তেমনই থাক। ও মূর্তি নিয়ে অত চিন্তা করিস না। যতদিন আমার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এখানে থাকবে, ততদিন ঐ মূর্তিও অবিকৃত অবস্থায় থাকবে।
সেই থেকে বহু ইতিহাসের সাক্ষি এই পীঠস্থান। অনেক ঝড়ঝাপটা অতিক্রম করে, প্রায় ১,০২৭ বছরেরও বেশী সময়(৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ২০২৪ সাল) ধরে একইভাবে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরখচিত বঙ্গের অন্যতম শাসকবংশ, “বিষ্ণুপুর মল্লরাজবংশ” প্রাচীন কুলদেবী “মা মৃন্ময়ী” বিরাজ করছেন। দেবীর আদি মন্দিরটি কেমন ছিলো, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না। বর্তমানে যে মন্দিরে দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, সেটি মল্লবংশের ৫৯তম উত্তরসূরী মহারাজ রামকৃষ্ণদেব(১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ- ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ) নির্মাণ করান। মন্দিরটিতে পাঁচখিলনের দালানে এবং সেখানে জগন্মাতার গর্ভগৃহের সামনাসামনিই রয়েছে সেই স্মৃতি বিজড়িত বেলগাছ। সেখানে আজও শারদোৎসবের ষষ্ঠ্যাদি বোধন বসে। মন্দিরের এলাকাটি বিরাট, কিন্তু শান্ত এবং একইসঙ্গে নীরব ইতিহাসের সাক্ষী। পাশেই একটি দীঘি আছে। সেখানকার জলেই দেবীর নিত্যসেবা, ভোগ ইত্যাদি হয়। মন্দিরের উত্তরদিকে(পিছনে) একটি ভাঙা পোড়োপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন, ঐটিই জগৎমল্ল প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ী। মন্দিরের গর্ভগৃহের একটু আগেই একটি কামান আছে। তাতে আগে তোপদাগা হ’তো, এর পাশাপাশি গোটা অঞ্চলে পূজোর শুভ সূচনা প্রচারের উদ্দেশ্যেই কামানটি দাগা হত।
মৃন্ময়ী এখানে সপরিবারে অধিষ্ঠিতা। তবে পরিবার সজ্জার ধরণটি আলাদা। সচরাচর, দেবীর দু’পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী থাকেন। তাঁদের নীচে অধিষ্ঠান করেন গণেশ ও কার্ত্তিক। এখানে দেবীর দু’পাশে গণেশ ও কার্ত্তিক রয়েছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী রয়েছেন নীচে। চালচিত্রের একেবারে উঁচুতে নন্দীভৃঙ্গী সেবিত দেবাদিদেব রয়েছেন। সম্পূর্ণ বিগ্রহটি মাটির তৈরী। প্রতিবছর অঙ্গরাগ করা হয়। একটানা হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে একটি মাটির বিগ্রহ অবিকৃত অবস্থায় পূজো গ্রহণ করে আসছেন। সারাবছরই কমবেশী ভক্তসমাগম হয়।
মল্লরাজাদের পূজো শুরু হয়, শুক্লা ষষ্ঠীর পনেরো(১৫)দিন আগে অর্থাৎ, কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ তিথিতে। সেদিন, স্থানীয় শিল্পীদের তৈরী দেবী পটেশ্বরী(বড় ঠাকুরাণী) মৃন্ময়ী মন্দিরে আসেন। শুরু হয়, ষোড়শোপচারে আরাধনা। একটানা পালা করে পুরোহিতরা যজ্ঞে আহুতি দিতে থাকতেন। শুক্লা ষষ্ঠীতে আসেন দ্বিতীয় পটেশ্বরী(মেজো ঠাকুরাণী)। মেজোঠাকুরাণীকে বটগাছের নীচেই প্রথমে স্থাপন করা হয়, প্রতীকি বিল্বশাখা রোপন করে বোধন অধিবাসের পরে মৃন্ময়ীর পাশে বসানো হয়।
সপ্তমীর দিন সকালে আসেন তৃতীয় পটেশ্বরী(ছোটো ঠাকুরাণী)। সঙ্গে তিনজন পটেশ্বরী ঠাকুরাণীর তিনটি আলাদা আলাদা নবপত্রিকা। মহাষ্টমী তিথির সন্ধিপূজায় একটি পিতলের গামলায় জল ভর্তি করে তাতে অতিসূক্ষ্ণ ছিদ্রবিশিষ্ট একটি বাটি ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ছিদ্রযুক্ত বাটিটি নাকি এমনভাবেই তৈরী যে জল ভর্তি হয়ে গামলায় ডুবে যেতে তার ২৪মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ, সন্ধিক্ষণেই সেটি ডুবে যায়। ডোবার সাথে সাথেই বলিদান শুরু হয়। মহাষ্টমীর মধ্যরাত্রে এখানে অর্ধরাত্র বিহিত পূজা হয়।
এই পূজোতেই কোনো এক সময়ে বিরোধী পক্ষীয় রাজা/তষ্কর/রাজবিরোধী/বিশ্বাসঘাতকদের ধরে আনা হতো। এমনকি তাকে/তাদেরকে বলিদান দেওয়া হ’তো। এখনও মন্দিরের গর্ভে একটি প্রাচীন কীটদষ্ট ক্ষয়ে যাওয়া যূপকাষ্ঠ রয়েছে, সেই নরবলির জলজ্যান্ত নীরর ইতিহাস বয়ে নিয়ে চলছে। এছাড়াও মহানবমীতে মহিষ সহ মেষ ও ছাগ বলিদানের নিময়ও ছিল। প্রতিপদের দিন প্রজ্জ্বলিত হওয়া যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়ে বিজয়াদশমীতে অগ্নি তথা তিনটি নবপত্রিকা সমেত তিন পটেশ্বরী ঠাকুরাণীর বিসর্জ্জন হত। কেবলমাত্র রাজকীয় জাঁকজমক ও বলিদান ছাড়া বাকী সব নিয়মই এখনও পালিত হয়ে আসছে।
১৬২২ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ বীরসিংহ মল্লের রাজত্ব থেকেই রাজধানীর মানচিত্রে বহু পটপরিবর্তন হয়। পরমবৈষ্ণব মহারাজ বৃন্দাবন তীর্থ ঘুরে আসার পরেই রাজধানীতে ‘নব বৃন্দাবন’ স্থাপনের মানসে একের পর এক মন্দির(মল্লেশ্বর, শ্যামরায়, জোড়াবাংলা), মঞ্চ(দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ), জলাশয়(রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড) নির্মাণ করাতে থাকেন। তাঁর আমলেই বিষ্ণুপুর ঘরানার ‘টেরাকোটা’ শিল্প ও উন্নতির চরম শিখরে স্থান পায়। মল্লবংশের ৫৩তম বংশধর মহারাজ দুর্জন সিংহদেব(১৬৮২ খ্রীস্টাব্দ- ১৭০২ খ্রীস্টাব্দ)-এর রাজত্বকালে পূর্বক্তো বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব আরও প্রাধান্য পেতে থাকে। মহারাজ দুর্জনও একজন বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি শ্রীশ্রী মদনমোহনের মন্দির স্থাপন(১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ) এবং শ্রীকৃষ্ণের নামানুযায়ী রাজ্যের নাম দেন “বাঁকাচূড়া” যা আজকে অপভ্রংশে “বাঁকুড়া” নামে পরিচিত। যদিও তাঁর আগে থেকেই বহু মল্লরাজা গণ বহু বৈষ্ণবীয় ঘরাণার মন্দির এবং বিগ্রহ স্থাপন করেছেন, কিন্তু মহারাজ দুর্জনের “মদনমোহন” এবং “দলমাদল” কামান সকলকে ছাপিয়ে গেছে। তিনিই মৃন্ময়ী মন্দিরে পশু বলিদানের নিয়ম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দে’ন। তার পরিবর্তে কুষ্মাণ্ড, আখ ইত্যাদি বলিদানের নিয়ম শুরু করেন।
বাংলার আদি দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় বিষ্ণপুরের মল্লরাজবংশের মা মৃন্ময়ী’র মন্দিরে